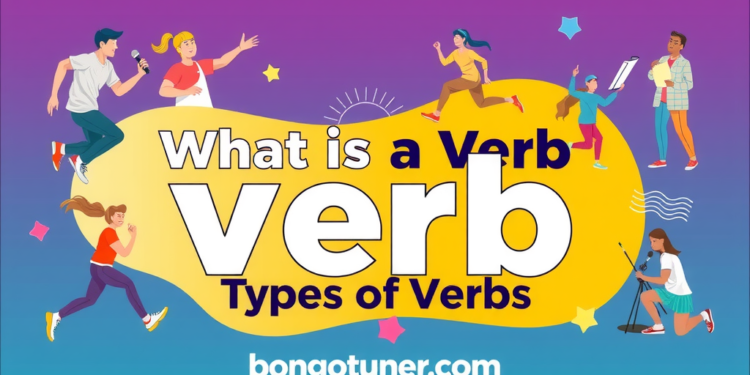আসসালামু আলাইকুম! কেমন আছেন সবাই? আজ আমরা বাংলা ব্যাকরণের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব – ক্রিয়া বা verb। ক্রিয়া ছাড়া কোনো বাক্যই সম্পূর্ণ হতে পারে না, তাই ক্রিয়া সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখাটা জরুরি। তাহলে চলুন, দেরি না করে জেনে নেই ক্রিয়া কাকে বলে, কত প্রকার ও কি কি!
ক্রিয়া (Verb) কি?
সহজ ভাষায় বলতে গেলে, কোনো কাজ করা বোঝানো হলেই সেটা ক্রিয়া। “যা করা হয়, তাই ক্রিয়া”। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে:
- আমি ভাত খাই। এই বাক্যে “খাই” হলো ক্রিয়া, কারণ এটি একটি কাজ করা বোঝাচ্ছে।
- পাখি আকাশে ওড়ে। এখানে “ওড়ে” ক্রিয়া, উড়বার কাজ বোঝাচ্ছে।
আরও কিছু উদাহরণ:
- পড়া
- লেখা
- খাওয়া
- দেখা
- শোনা
- যাওয়া
- আসা
ক্রিয়া কত প্রকার ও কি কি?
বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়াকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। এদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগ নিচে আলোচনা করা হলো:
কর্মের ভিত্তিতে ক্রিয়ার প্রকারভেদ
কর্ম মানে হলো object। বাক্যের ক্রিয়াটি কোনো কর্মের উপর নির্ভরশীল কিনা, তার উপর ভিত্তি করে ক্রিয়া দুই প্রকার:
সকর্মক ক্রিয়া (Transitive Verb)
যে ক্রিয়ার কর্ম (object) থাকে, তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ, ক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার জন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন হয়।
উদাহরণ:
- আমি বই পড়ি। এখানে “পড়ি” ক্রিয়াটি “বই” কর্মের উপর নির্ভরশীল। যদি প্রশ্ন করা হয়, “আমি কী পড়ি?” উত্তর আসবে “বই”।
অকর্মক ক্রিয়া (Intransitive Verb)
যে ক্রিয়ার কর্ম (object) থাকে না, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। ক্রিয়াটি নিজেই সম্পূর্ণ, এর জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না।
উদাহরণ:
- পাখি ওড়ে। এখানে “ওড়ে” ক্রিয়াটির কোনো কর্ম নেই। “পাখি কী ওড়ে?” – এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।
গঠন অনুসারে ক্রিয়ার প্রকারভেদ
গঠন অনুসারে ক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:
মৌলিক ক্রিয়া বা সরল ক্রিয়া (Simple Verb)
যে ক্রিয়া একটি মাত্র মূল ধাতু দিয়ে গঠিত, তাকে মৌলিক ক্রিয়া বলে। এগুলো সাধারণত কোনো প্রকার বিভক্তি ছাড়াই ব্যবহৃত হয়।
উদাহরণ:
- যা, খা, দে, পড়, শো ইত্যাদি। যেমন: আমি যাব, তুমি খাবে, সে দেবে, আমরা পড়ি, তারা শোনে।
যৌগিক ক্রিয়া (Compound Verb)
যখন দুইটি ধাতু বা ক্রিয়া একসাথে মিলিত হয়ে একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে।
উদাহরণ:
- যাওয়া + হওয়া = যাওয়া হওয়া (যেমন: কাজটি করা যাওয়া হলো।)
- দেখা + করা = দেখা করা (যেমন: তার সাথে আমার দেখা করা দরকার।)
- বলা + ওঠা = বলে ওঠা(যেমন: কথাটা সে বলেই উঠলো।)
অর্থের বিচারে ক্রিয়ার প্রকারভেদ
অর্থের বিচারে ক্রিয়াকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো:
সমাপিকা ক্রিয়া (Finite Verb)
যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ, এই ক্রিয়া ব্যবহার করলে বাক্যটি সম্পূর্ণ হয় এবং শ্রোতার মনে আর কোনো প্রশ্ন থাকে না।
উদাহরণ:
- আমি ভাত খাই।
- সে স্কুলে যায়।
অসমাপিকা ক্রিয়া (Non-finite Verb)
যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। এই ক্রিয়া ব্যবহার করলে বাক্যটি অসম্পূর্ণ থাকে এবং আরও কিছু শোনার বা জানার আগ্রহ থাকে।
উদাহরণ:
- আমি ভাত খেতে… (পুরো অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে না)
- সে স্কুলে গিয়ে… (আরও কিছু শোনার অপেক্ষা থাকে)
অসমাপিকা ক্রিয়া সাধারণত বাক্যের শেষে থাকে না এবং এর সাথে “তে”, “লে”, “এ” ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত থাকে। যেমন: খেতে, গেলে, গিয়ে ইত্যাদি।
সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার পার্থক্য কিভাবে বুঝব?
সকর্মক ক্রিয়া চেনার সহজ উপায় হলো, ক্রিয়াকে “কী” বা “কাকে” দিয়ে প্রশ্ন করলে যদি কোনো উত্তর পাওয়া যায়, তাহলে সেটি সকর্মক ক্রিয়া। আর যদি কোনো উত্তর না পাওয়া যায়, তাহলে সেটি অকর্মক ক্রিয়া।
উদাহরণ:
- সে বই পড়ে। (সে কী পড়ে? উত্তর: বই) – এটি সকর্মক ক্রিয়া।
- পাখি ওড়ে। (পাখি কী ওড়ে? কোনো উত্তর নেই) – এটি অকর্মক ক্রিয়া।
অন্যান্য প্রকারভেদ
এছাড়াও, আরও কিছু প্রকারভেদ রয়েছে, যা আমাদের জানা দরকার:
প্রযোজক ক্রিয়া (Causative Verb)
যখন কোনো কর্তা নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে করায়, তখন সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।
উদাহরণ:
- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এখানে মা নিজে দেখছেন না, শিশুকে দেখাচ্ছেন।
- শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। শিক্ষক নিজে পড়ছেন না, ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।
নামধাতুর ক্রিয়া (Nominal Verb)
বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে “আ” প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু গঠিত হয়, এবং সেই ধাতু দিয়ে গঠিত ক্রিয়াকে নামধাতুর ক্রিয়া বলে।
উদাহরণ:
- ঘুম থেকে ঘুমা > ঘুমাচ্ছে (ছেলেটি ঘুমাচ্ছে।)
- বেত থেকে বেতা > বেতাচ্ছে (ছেলেটি খুব বেতাচ্ছে।)
মিশ্র ক্রিয়া ( संयुक्त क्रिया )
বিশেষ্য, বিশেষণ ও অনুকার অব্যয়ের সঙ্গে √কর্, √দে, √পা, √যা, √খা, √রাখ, √হ’ ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াকে মিশ্র ক্রিয়া বলে।
যেমন : ভয় কর্, ভালো হ, পড়া দে, রাজি হ, ইত্যাদি।
- তাকে দেখে আমার খুব দয়া হলো।
- মাথা ঝিমঝিম করছে।
যৌগিক ক্রিয়া ও মিশ্র ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি?
যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয় দুটি ক্রিয়া বা ধাতু দিয়ে, যেখানে উভয় ক্রিয়ার নিজস্ব অর্থ থাকে এবং তারা মিলিতভাবে একটি নতুন অর্থ তৈরি করে। অন্যদিকে, মিশ্র ক্রিয়া গঠিত হয় একটি বিশেষ্য, বিশেষণ বা অব্যয়ের সাথে একটি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে, যেখানে বিশেষ্য বা বিশেষণটি ক্রিয়ার অর্থকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।
সহযোগী ক্রিয়া
যে ক্রিয়া অন্য ক্রিয়াকে বিশেষভাবে সাহায্য করে বা তার অর্থের দ্যোতনা বৃদ্ধি করে, তাকে সহযোগী ক্রিয়া বলে। সহযোগী ক্রিয়াগুলো প্রধান ক্রিয়ার সাথে বসে কালের অর্থ, প্রকার বা ভাবের ভিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে।
যেমন:
- সে গান গাইছে। – এখানে ‘গাইছে’ হলো প্রধান ক্রিয়া এবং ‘ছে’ হলো সহযোগী ক্রিয়া, যা বর্তমান কালের অবিরামতা বোঝাচ্ছে।
- আমি কাজটি করে ফেলেছি। – এখানে ‘করেছি’ হলো প্রধান ক্রিয়া এবং ‘ফেলেছি’ হলো সহযোগী ক্রিয়া, যা কাজটি শেষ হয়েছে বোঝাচ্ছে।
- তিনি বক্তৃতা দিতে লাগলেন। – এখানে ‘দিতে’ হলো প্রধান ক্রিয়া এবং ‘লাগলেন’ হলো সহযোগী ক্রিয়া, যা কাজের শুরু বা আগ্রহ বোঝাচ্ছে।
সহযোগী ক্রিয়া সাধারণত প্রধান ক্রিয়ার পরে বসে এবং এটি প্রধান ক্রিয়ার কালের রূপ পরিবর্তনে সাহায্য করে।
ক্রিয়া পদের উদাহরণ
বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া পদের উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:
- সকর্মক ক্রিয়া: আমি ভাত খাই। (এখানে “খাই” সকর্মক ক্রিয়া)
- অকর্মক ক্রিয়া: সে হাসে। (এখানে “হাসে” অকর্মক ক্রিয়া)
- সমাপিকা ক্রিয়া: তিনি গান করেন। (এখানে “করেন” সমাপিকা ক্রিয়া)
- অসমাপিকা ক্রিয়া: আমি গিয়ে দেখব। (এখানে “গিয়ে” অসমাপিকা ক্রিয়া)
- প্রযোজক ক্রিয়া: মা শিশুকে ঘুম পাড়াচ্ছেন। (এখানে “ঘুম পাড়াচ্ছেন” প্রযোজক ক্রিয়া)
“ধাতু” এবং “ক্রিয়া”-এর মধ্যে আসলে সম্পর্কটা কী?
ধাতু হলো ক্রিয়ার মূল অংশ। ক্রিয়া পদ গঠনের সময় ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া পদ তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, “পড়” একটি ধাতু। এর সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে আমরা “পড়ি”, “পড়বে”, “পড়েছিলাম”-এর মতো ক্রিয়া পদ তৈরি করতে পারি।
ক্রিয়া ব্যবহারের কিছু টিপস
- বাক্যের অর্থ পরিষ্কার করার জন্য সঠিক ক্রিয়া ব্যবহার করুন।
- কর্তা ও কর্মের সাথে সঙ্গতি রেখে ক্রিয়া ব্যবহার করুন।
- অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করার সময় খেয়াল রাখুন, যেন বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ না থাকে।
অনুশীলন
নিচের বাক্যগুলোতে ক্রিয়া চিহ্নিত করুন এবং সেটি কোন প্রকার, তা উল্লেখ করুন:
- আমি ছবি আঁকি।
- বৃষ্টি পড়ছে।
- শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।
- সে গান গেয়েছিল।
- তোমরা খেলতে যাও।
উত্তর:
- আঁকি (সকর্মক, সমাপিকা)
- পড়ছে (অকর্মক, সমাপিকা)
- পড়াচ্ছেন (প্রযোজক, সমাপিকা)
- গেয়েছিল (অকর্মক, সমাপিকা)
- যেতে (অসমাপিকা), যাও (অকর্মক, সমাপিকা)
আশা করি, আজকের আলোচনা থেকে ক্রিয়া সম্পর্কে আপনার ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। ব্যাকরণের আরও অনেক মজার বিষয় নিয়ে সামনে আমরা আলোচনা করব।
FAQ সেকশন
এই অংশে ক্রিয়া সম্পর্কিত কিছু সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হলো:
ক্রিয়া পদের মূল অংশকে কী বলে?
ক্রিয়া পদের মূল অংশকে ধাতু বলে। এই ধাতুর সঙ্গেই বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া পদ গঠিত হয়।
কোন ক্রিয়ার কর্ম থাকে না?
অকর্মক ক্রিয়ার কর্ম থাকে না। এই ক্রিয়াগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্য কোনো কর্মের উপর নির্ভরশীল নয়।
ক্রিয়ার কাল বলতে কী বোঝায়?
ক্রিয়ার কাল হলো ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়। এটি বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ হতে পারে।
অসমাপিকা ক্রিয়া চেনার উপায় কী?
অসমাপিকা ক্রিয়া চেনার সহজ উপায় হলো, এটি বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে না এবং এর সাথে “তে”, “লে”, “এ” ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত থাকে।
যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ দিন।
যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ: “সে গান গেয়ে উঠলো।” এখানে “গেয়ে উঠলো” হলো যৌগিক ক্রিয়া।
উপসংহার
তাহলে আজ আমরা জানলাম ক্রিয়া কাকে বলে, কত প্রকার ও কি কি এবং তাদের ব্যবহারবিধি। বাংলা ব্যাকরণের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ভালোভাবে বুঝতে পারলে বাক্য গঠন এবং ভাষার ব্যবহার আরও সহজ হবে।
যদি এই বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি মনে হয় এই লেখাটি আপনার বন্ধুদের উপকারে লাগবে, তাহলে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন! আল্লাহ হাফেজ!