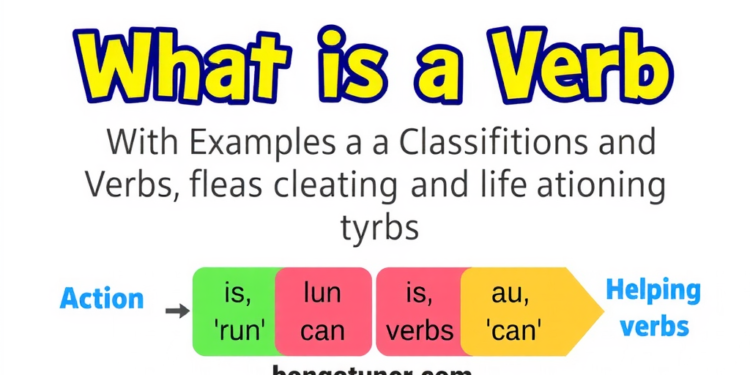ক্রিয়াপদ: সংজ্ঞা, উদাহরণ এবং শ্রেণীবিভাগ – বাংলা ব্যাকরণের একটি অপরিহার্য অংশ
বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়াপদের গুরুত্ব অপরিসীম। বাক্যকে সম্পূর্ণতা দিতে এবং মনের ভাব প্রকাশ করতে ক্রিয়াপদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। “মাছেরা ঝাঁক বেঁধে সাঁতার কাটে” অথবা “পাখিরা আকাশে উড়ে বেড়ায়” – এই বাক্যগুলোতে ‘সাঁতার কাটে’ এবং ‘উড়ে বেড়ায়’ শব্দগুলোই হলো ক্রিয়াপদ। এগুলো না থাকলে বাক্যগুলো অর্থহীন হয়ে যেত।
এই ব্লগ পোস্টে আমরা ক্রিয়াপদ কাকে বলে, এর প্রকারভেদ এবং বাংলা ব্যাকরণে এর তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তাহলে চলুন, শুরু করা যাক!
ক্রিয়াপদ কাকে বলে?
ক্রিয়াপদ হলো সেই শব্দ যা কোনো কাজ করা, হওয়া বা ঘটা বোঝায়। অর্থাৎ, যে পদ দ্বারা কোনো কিছু করা, হওয়া, ঘটা, চলা, বলা ইত্যাদি বোঝানো হয়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। ক্রিয়াপদ ছাড়া কোনো বাক্য সম্পূর্ণ হতে পারে না।
সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ক্রিয়াপদ হলো বাক্যের প্রাণ। এটা ছাড়া যেমন মানুষের জীবন অচল, তেমনি ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্যও অচল।
উদাহরণ:
- আমি ভাত খাই।
- সে গান গায়।
- বৃষ্টি হচ্ছে।
- বাবা বাজার গিয়েছেন।
উপরের উদাহরণগুলোতে খাই, গায়, হচ্ছে, গিয়েছেন – এই শব্দগুলো ক্রিয়াপদ।
ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ
ক্রিয়াপদকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিচে প্রধান কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা হলো:
কর্মের ভিত্তিতে ক্রিয়াপদ
কর্মের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে ক্রিয়াপদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া।
সকর্মক ক্রিয়া (Transitive Verb)
যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ, ক্রিয়াটি কাকে বা কী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।
উদাহরণ:
- আমি বই পড়ি। (কী পড়ি? – বই)
- সে ভাত খায়। (কী খায়? – ভাত)
- বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন। (কাকে দিয়েছেন? – আমাকে)
এখানে “বই”, “ভাত” এবং “আমাকে” হলো কর্মপদ। এইজন্য “পড়ি”, “খায়” ও “কিনে দিয়েছেন” সকর্মক ক্রিয়া।
অকর্মক ক্রিয়া (Intransitive Verb)
যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে না, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। এই ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি কী বা কাকে প্রশ্নের উত্তর দেয় না।
উদাহরণ:
- পাখি ওড়ে।
- ছেলেটি কাঁদে।
- বৃষ্টি পড়ছে।
- সে হাসে।
এই উদাহরণগুলোতে “ওড়ে”, “কাঁদে”, “পড়ছে” এবং “হাসে” – এগুলো কোনো কর্মকে নির্দেশ করে না, তাই এগুলো অকর্মক ক্রিয়া।
গঠনের ভিত্তিতে ক্রিয়াপদ
গঠন অনুসারে ক্রিয়াপদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: মৌলিক বা সরল ক্রিয়া এবং যৌগিক বা মিশ্র ক্রিয়া।
মৌলিক বা সরল ক্রিয়া (Simple Verb)
যে ক্রিয়া একটি মাত্র শব্দ দিয়ে গঠিত, তাকে মৌলিক বা সরল ক্রিয়া বলে। এগুলোকে বিশ্লেষণ করা যায় না।
উদাহরণ:
- যা, খা, পড়, শো, বস, দেখ, ইত্যাদি।
যেমন:
- আমি যাই।
- সে খায়।
- তুমি পড়।
যৌগিক বা মিশ্র ক্রিয়া (Compound Verb)
যখন একটি সমাপিকা ক্রিয়া একটি অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে।
উদাহরণ:
- তিনি বলতে লাগলেন।
- বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো।
- ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়ল।
এখানে “বলতে লাগলেন”, “পড়তে শুরু করলো” এবং “ঘুমিয়ে পড়ল” হলো যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ।
অর্থের ভিত্তিতে ক্রিয়াপদ
অর্থের দিক থেকে ক্রিয়াপদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন:
সমাপিকা ক্রিয়া (Finite Verb)
যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। এই ক্রিয়া বাক্যের সমাপ্তি ঘোষণা করে।
উদাহরণ:
- আমি ভাত খাই।
- সে স্কুলে যায়।
- তারা খেলছে।
“খাই”, “যায়”, “খেলছে” – এই ক্রিয়াগুলো বাক্যগুলোকে সম্পূর্ণতা দিচ্ছে, তাই এগুলো সমাপিকা ক্রিয়া।
অসমাপিকা ক্রিয়া (Non-finite Verb)
যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। এই ক্রিয়া বাক্যের সমাপ্তি ঘটায় না, বরং আরও কিছু বলার অপেক্ষা রাখে।
উদাহরণ:
- আমি ভাত খেয়ে…
- সে স্কুলে গিয়ে…
- তারা খেলতে…
“খেয়ে”, “গিয়ে”, “খেলতে” – এই ক্রিয়াগুলো বাক্যগুলোকে অসম্পূর্ণ রাখছে, তাই এগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া।
প্রযোজক ক্রিয়া (Causative Verb)
যখন কোনো কর্তা নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে করায়, তখন সেই ক্রিয়াপদকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।
উদাহরণ:
- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।
- শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।
- বাবা আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন।
এখানে, “দেখাচ্ছেন”, “পড়াচ্ছেন”, “করাচ্ছেন” – এই ক্রিয়াগুলো প্রযোজক ক্রিয়া, কারণ কর্তা নিজে কাজটি না করে অন্যকে দিয়ে করাচ্ছে।
নামধাতুর ক্রিয়া
বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে ‘আ’ প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু গঠিত হয়, সেই ধাতুকে নামধাতু বলে। আর এই নামধাতু দিয়ে গঠিত ক্রিয়াই হলো নামধাতুর ক্রিয়া।
উদাহরণ:
- বেত মারাও (বেত + আ)।
- ঘুড়ি বাঁজাও (বাঁ + আ)।
- তাকে দেখে ঘৃণাচ্ছ (ঘৃণা + আ)।
যৌগিক ক্রিয়ার প্রকারভেদ
যৌগিক ক্রিয়া বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার আলোচনা করা হলো:
- অভ্যস্ততা অর্থে: সে রোজ সকালে গান করে থাকে।
- সম্ভাব্যতা অর্থে: এমন ঘটনা ঘটতে পারে।
- অনুমতি অর্থে: এখন তোমরা যেতে পারো।
- অনিবার্যতা অর্থে: আমাকে কাজটি করতেই হবে।
- ** আকস্মিকতা অর্থে:** লোকটি মরতে বসলো।
বাচ্যের ভিত্তিতে ক্রিয়াপদ
বাচ্য মানে হলো কথা বলার ভঙ্গি বা প্রকার। বাচ্যের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াপদ তিন প্রকার:
- কর্তৃবাচ্য (Active Voice)
- কর্মবাচ্য (Passive Voice)
- ভাববাচ্য (Impersonal Voice)
কর্তৃবাচ্য
কর্তৃবাচ্যে কর্তা প্রধান এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয়।
উদাহরণ:
- আমি বই পড়ি।
- সে গান গায়।
কর্মবাচ্য
কর্মবাচ্যে কর্ম প্রধান এবং ক্রিয়াপদ কর্মের অনুসারী হয়।
উদাহরণ:
- আমার দ্বারা বই পঠিত হয়।
- তার দ্বারা গান গাওয়া হয়।
ভাববাচ্য
ভাববাচ্যে ক্রিয়ার ভাব প্রধান এবং এখানে কর্তা গৌণ থাকে।
উদাহরণ:
- আমার যাওয়া হবে না।
- তোমাকে যেতে হবে।
ক্রিয়াপদের কাল (Tense)
ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কে কাল বলে। কাল প্রধানত তিন প্রকার:
- বর্তমান কাল (Present Tense)
- অতীত কাল (Past Tense)
- ভবিষ্যৎ কাল (Future Tense)
প্রত্যেকটি কালের আবার বিভিন্ন রূপ আছে, যা ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন সময় এবং অবস্থাকে নির্দেশ করে।
বর্তমান কাল
বর্তমানকালে কোনো কাজ বর্তমানে হচ্ছে বা হয়, এমন বোঝায়।
উদাহরণ:
- আমি পড়ি। (সাধারণ বর্তমান)
- আমি পড়ছি। (ঘটমান বর্তমান)
- আমি পড়েছি। (পুরাঘটিত বর্তমান)
- আমি পড়ছি কিছুক্ষণ ধরে। (ঘটমান পুরাঘটিত বর্তমান)
অতীত কাল
অতীতকালে কোনো কাজ আগে হয়েছে, এমন বোঝায়।
উদাহরণ:
- আমি পড়েছিলাম। (সাধারণ অতীত)
- আমি পড়ছিলাম। (ঘটমান অতীত)
- আমি পড়েছি। (পুরাঘটিত অতীত)
- আমি পড়ছিলাম কিছুক্ষণ ধরে। (ঘটমান পুরাঘটিত অতীত)
ভবিষ্যৎ কাল
ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ পরে হবে, এমন বোঝায়।
উদাহরণ:
- আমি পড়ব। (সাধারণ ভবিষ্যৎ)
- আমি পড়তে থাকব। (ঘটমান ভবিষ্যৎ)
- আমি পড়ে থাকব। (পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ)
বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়াপদের গুরুত্ব
বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়াপদের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করা হলো:
- ক্রিয়াপদ ছাড়া কোনো বাক্য গঠিত হতে পারে না।
- এটি বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে এবং বক্তার মনোভাব প্রকাশ করে।
- ক্রিয়াপদের মাধ্যমে কালের ধারণা পাওয়া যায়, যা ঘটনা বা কাজের সময় নির্দেশ করে।
- ক্রিয়াপদ বাক্যকে গতিশীল করে এবং বর্ণনাকে জীবন্ত করে তোলে।
ক্রিয়াপদ চেনার সহজ উপায়
ক্রিয়াপদ চেনার জন্য কিছু সহজ উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে:
- বাক্যের মধ্যে ‘করা’, ‘হওয়া’, ‘যাওয়া’, ‘খাওয়া’ ইত্যাদি শব্দ খুঁজে বের করুন।
- দেখুন শব্দটি দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে কিনা।
- ক্রিয়াপদ সাধারণত বাক্যের শেষে বা কাছাকাছি থাকে।
ক্রিয়াপদ নিয়ে কিছু সাধারণ ভুল
ক্রিয়াপদ ব্যবহারের সময় কিছু সাধারণ ভুল প্রায়ই দেখা যায়। নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:
- অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করা।
- সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা।
- কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের ক্রিয়াপদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারা।
- কালের সঠিক ব্যবহার না করা।
এই ভুলগুলো এড়িয়ে যেতে পারলে ক্রিয়াপদ ব্যবহার আরও নির্ভুল হবে।
ক্রিয়াপদ সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)
এখানে ক্রিয়াপদ নিয়ে কিছু সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হলো:
প্রশ্ন: সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে, যেখানে অসমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে না।
প্রশ্ন: প্রযোজক ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
উত্তর: যখন কোনো কর্তা নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে করায়, তখন সেই ক্রিয়াপদকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। উদাহরণ: মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।
প্রশ্ন: সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ দিন।
উত্তর: সকর্মক ক্রিয়া: আমি বই পড়ি। (এখানে ‘বই’ কর্মপদ)। অকর্মক ক্রিয়া: পাখি ওড়ে। (এখানে কোনো কর্মপদ নেই)।
প্রশ্ন: ধাতু কাকে বলে?
উত্তর: ক্রিয়াপদের মূল অংশকে ধাতু বলে। যেমন: √যা, √খা, √পড় ইত্যাদি।
প্রশ্ন: ক্রিয়াপদের কাল বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: ক্রিয়াপদের কাল হলো ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়। এটি বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ হতে পারে।
ক্রিয়াপদের ব্যবহারিক প্রয়োগ
ক্রিয়াপদের সঠিক ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:
- একটি সঠিক ইমেল লিখতে ক্রিয়াপদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার।
- প্রতিবেদনে ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা বোঝাতে ক্রিয়াপদের কাল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
- যোগাযোগের ক্ষেত্রে, আমরা কী করছি বা কী করতে যাচ্ছি, তা বোঝাতে ক্রিয়াপদের ভূমিকা অপরিহার্য।
ক্রিয়াপদের আরও কিছু উদাহরণ
- বৃষ্টি পড়ছে (অকর্মক ক্রিয়া)।
- আমি ছবি আঁকি (সকর্মক ক্রিয়া)।
- শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন (প্রযোজক ক্রিয়া)।
- সে গান গাইতে শুরু করল (যৌগিক ক্রিয়া)।
- তোমাকে যেতে হবে (ভাববাচ্য)।
উপসংহার
ক্রিয়াপদ বাংলা ব্যাকরণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্রিয়াপদ কাকে বলে (kriyapad kake bole), এর প্রকারভেদ, উদাহরণ এবং ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার মাধ্যমে, আমরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। ক্রিয়াপদের সঠিক ব্যবহার বাক্যকে অর্থবহ এবং সুস্পষ্ট করে তোলে। তাই, বাংলা ভাষা শিখতে এবং ব্যবহার করতে ক্রিয়াপদের জ্ঞান অপরিহার্য।
আশা করি, এই ব্লগ পোস্টটি ক্রিয়াপদ সম্পর্কে আপনার ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়ক হয়েছে। কোনো প্রশ্ন থাকলে বা আরও কিছু জানতে চাইলে, নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আপনার ব্যাকরণচর্চা আরও সুন্দর হোক, এই কামনায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ!