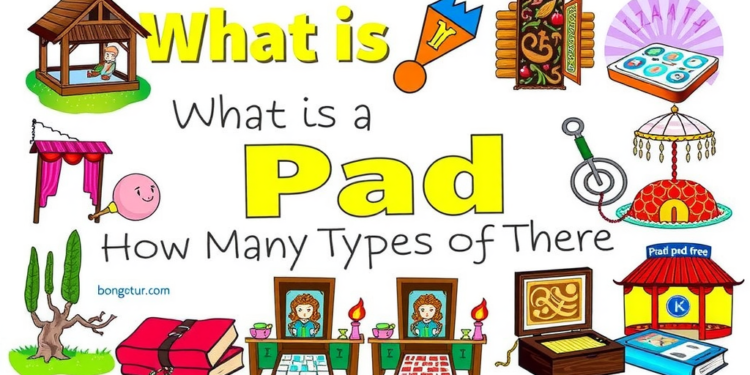আচ্ছা, ব্যাকরণের কচকচিতে মন নেই তো? ভাবছেন, “ধুর, পদ আবার কী জিনিস!” তাহলে বলি শুনুন, এই পদই কিন্তু ভাষার প্রাণ। একটা বাক্যের ভিত গড়ে তোলে এই পদগুলোই। তাই, বাংলা ব্যাকরণকে ভালো করে বুঝতে গেলে, পদের হাল-হকিকত জানাটা খুব জরুরি। আজ আমরা এই পদ নিয়ে সহজভাবে আলোচনা করব, যাতে ব্যাকরণের জটিলতা আপনার কাছে ডাল-ভাত হয়ে যায়।
পদ কাকে বলে? (Pod Kake Bole?)
সহজ ভাষায় বলতে গেলে, বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি পদ। “আমি ভাত খাই” – এই বাক্যে “আমি”, “ভাত”, “খাই” প্রত্যেকটি এক একটি পদ। পদ ছাড়া কোনো বাক্য তৈরি হতে পারে না!
ব্যাকরণের ভাষায়, “বাক্যস্থিত প্রত্যেকটি অর্থবোধক শব্দকে পদ বলে।”
পদ কত প্রকার ও কী কী? (Pod Koto Prokar o Ki Ki?)
পদ প্রধানত পাঁচ প্রকার:
১. বিশেষ্য পদ (Bisheshyo Pod)
২. বিশেষণ পদ (Bisheshon Pod)
৩. সর্বনাম পদ (Sarbonam Pod)
৪. অব্যয় পদ ( অব্যয় Pod)
৫. ক্রিয়া পদ (Kriya Pod)
চলুন, এই পদগুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।
বিশেষ্য পদ (Bisheshyo Pod): নামের মহিমা
কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, জাতি, গুণ, অবস্থা বা কাজের নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে। বিশেষ্য পদ মানেই নাম! আপনার নাম, আমার নাম, নদীর নাম, পাহাড়ের নাম – সবই বিশেষ্য।
বিশেষ্য পদের প্রকারভেদ (Bisheshyo Pod er Prokarভেদ):
বিশেষ্য পদকে সাধারণত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়:
-
নামবাচক বিশেষ্য (Namবাচক Bisheshyo): কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, স্থান, নদী, পর্বত, সমুদ্র, ইত্যাদির নাম। যেমন: ঢাকা, পদ্মা, হিমালয়, রবীন্দ্রনাথ।
- ব্যক্তির নাম : সাকিব আল হাসান, কাজী নজরুল ইসলাম
- স্থানের নাম: রুপগঞ্জ, সোনারগাঁও
- নদীর নাম: মেঘনা, যমুনা
- গ্রন্থের নাম: গীতাঞ্জলী, অগ্নিবীণা
-
জাতিবাচক বিশেষ্য (Jatবাচক Bisheshyo): কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে বোঝায়। যেমন: মানুষ, পাখি, গরু, বাঙালি।
- যেমন- মানুষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, মোরগ, ঘোড়া, হাতি, সিংহ ইত্যাদি।
-
বস্তুবাচক বিশেষ্য (Bastবাচক Bisheshyo): কোনো বস্তু বা জিনিসকে বোঝায়। যেমন: বই, খাতা, টেবিল, মাটি, পানি, সোনা, রুপা।
- যেমন- চাল, ডাল, লবণ, চিনি, পানি, মাটি, পাথর, লোহা, তামা, সোনা, রূপা ইত্যাদি।
-
গুণবাচক বিশেষ্য (Gunবাচক Bisheshyo): কোনো দোষ বা গুণকে বোঝায়। যেমন: তারুণ্য, সৌরভ, তিক্ততা, তারল্য।
- যেমন- লবণাক্ত, তিক্ততা, মধুরতা, তারল্য, সৌরভ, যৌবন, তারুণ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।
-
সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Samastiবাচক Bisheshyo): অনেকগুলো ব্যক্তি বা বস্তুর সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন: দল, সভা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল।
- যেমন- দল, সভা, সমিতি, ঝাঁক, বহর, পঞ্চায়েত ইত্যাদি।
-
ভাববাচক বিশেষ্য (Bhabবাচক Bisheshyo): কোনো কাজের ভাব বা ক্রিয়ার অবস্থাকে বোঝায়। যেমন: দর্শন, ভোজন, শয়ন, গমন।
- যেমন- গমন, দর্শন, ভোজন, শয়ন, স্মরন, কান্না, হাসি ইত্যাদি।
বিশেষণ পদ (Bisheshon Pod): গুণগান আর পরিচয়
যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়া পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা বা পরিমাণ বোঝায়, তাকে বিশেষণ পদ বলে। এটা অনেকটা বিশেষ্যের ‘গুণ-কীর্তন’ করার মতো!
“নীল আকাশ” – এখানে “নীল” শব্দটি আকাশের গুণ বোঝাচ্ছে। তাই এটি বিশেষণ পদ।
বিশেষণ পদের প্রকারভেদ (Bisheshon Pod er Prokarভেদ):
বিশেষণ পদ প্রধানত দুই প্রকার:
-
নাম-বিশেষণ (Nam-bisheshon): যে বিশেষণ পদ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে নাম-বিশেষণ বলে।
- রূপবাচক: সবুজ মাঠ, নীল আকাশ।
- গুণবাচক: দক্ষ কর্মী, সৎ মানুষ। এখানে দক্ষ ও সৎ শব্দ দুটি গুণবাচক বিশেষণ।
- সংখ্যাবাচক: দশ জন লোক, প্রথম শ্রেণি। এখানে দশ ও প্রথম শব্দ দুটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ।
- পরিমাণবাচক: অনেক চিনি, অল্প জল। এখানে অনেক ও অল্প শব্দ দুটি পরিমাণবাচক বিশেষণ।
-
ক্রিয়া-বিশেষণ (Kriya-bisheshon): যে বিশেষণ পদ ক্রিয়া পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ বলে।
- ধীরে ধীরে চল (কীভাবে চলছে?)।
- সে দ্রুত দৌড়ায় (কেমন দৌড়ায়?)।
- বৃষ্টি জোরে পড়ছে (কেমন পড়ছে?)।
সর্বনাম পদ (Sarbonam Pod): নামের প্রতিনিধি
বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। বারবার একই নাম ব্যবহার না করে, নামের বদলে অন্য যে শব্দ ব্যবহার করি, সেটাই সর্বনাম।
যেমন: “আরিফ ভালো ছেলে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়।” এখানে “সে” হলো সর্বনাম পদ, যা আরিফের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।
সর্বনাম পদের প্রকারভেদ (Sarbonam Pod er Prokarভেদ):
বাংলা ব্যাকরণে সর্বনাম পদকে সাধারণত ১০ ভাগে ভাগ করা হয়:
- ব্যক্তিবাচক সর্বনাম (Byaktiবাচক Sarbonam): আমি, তুমি, সে, তারা, আমরা, তোমরা, তিনি, আপনি, তাঁরা – এগুলো ব্যক্তিবাচক সর্বনাম।
- আত্মবাচক সর্বনাম (Atmabachak Sarbonam): স্বয়ং, নিজ, আপনি – এগুলো আত্মবাচক সর্বনাম। যেমন: সে স্বয়ং কাজটি করেছে।
- নির্দেশক সর্বনাম (Nirdeshak Sarbonam): এই, ঐ, এটা, ওটা, ইনি, উনি – এগুলো কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করে বোঝায়। যেমন: এই কলমটি আমার।
- সাকুল্যবাচক সর্বনাম (sakulyabachak Sarbonam): সব, সকলে, সবাই – এগুলো সাকুল্যবাচক সর্বনাম। যেমন: সভায় সকলে উপস্থিত ছিলেন।
- প্রশ্নবাচক সর্বনাম (Proshnobachak Sarbonam): কে, কী, কাকে, কার, কী, কোথায়, কখন – এগুলো প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন: তুমি কী চাও?
- অনির্দিষ্টবাচক সর্বনাম (Anirdistabachak Sarbonam): কেউ, কিছু, একজন, কোনো, কিছু একটা – এগুলো অনির্দিষ্টভাবে বোঝায়। যেমন: কেউ একজন দরজা ধাক্কাচ্ছে।
- সম্বন্ধবাচক সর্বনাম (Sambandhabachak Sarbonam): যে, যিনি, যা, যারা – এগুলো দুটি বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। যেমন: যে পরিশ্রম করে, সে ফল পায়।
- অনাদিবাচক সর্বনাম (Anadibachak Sarbanam): অন্য, পর – এগুলো অনাদিবাচক সর্বনাম। যেমন: পরের জন্য কুয়ো খুঁড়লে, নিজে পড়বি।
- ব্যতিহারিক সর্বনাম (Byatiharik Sarbanam): নিজেকে, নিজের – এগুলো ব্যতিহারিক সর্বনাম। যেমন: তিনি নিজেকে খুব পণ্ডিত মনে করেন।
- সংযোগবাচক সর্বনাম (Sanjogbachak Sarbanam): যা, যিনি – এগুলো সংযোগবাচক সর্বনাম। যেমন: যিনি আজকে আসবেন, তিনি আমার বন্ধু।
অব্যয় পদ ( অব্যয় Pod): যার কোনো পরিবর্তন নেই
যে পদের কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ লিঙ্গ, বচন, কারক ভেদে যার রূপ বদলায় না, তাকে অব্যয় পদ বলে। এগুলোর নিজের কোনো অর্থ নেই, কিন্তু বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
যেমন: এবং, কিন্তু, অথবা, ও, আর, হ্যাঁ, না, যদি, তবে, যদিও, তবুও – এই শব্দগুলো সব সময় একই থাকে।
“আমি এবং তুমি যাব” – এখানে “এবং” হলো অব্যয় পদ।
অব্যয় পদের প্রকারভেদ ( অব্যয় Pod er Prokarভেদ):
অব্যয় পদকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়:
- সংযোজক অব্যয় (Sanjojak অব্যয়): যে অব্যয় একাধিক শব্দ বা বাক্যকে যুক্ত করে, তাকে সংযোজক অব্যয় বলে। যেমন: এবং, ও, আর, কিন্তু, অথবা। উদাহরণ: রহিম ও করিম দুই ভাই।
- বিয়োজক অব্যয় (Bijojak অব্যয়): যে অব্যয় দুটি জিনিসের মধ্যে বিয়োগ বা বিকল্প বোঝায়, তাকে বিয়োজক অব্যয় বলে। যেমন: অথবা, নতুবা, কি। উদাহরণ: তুমি চা খাবে অথবা কফি?
- অনন্বয়ী অব্যয় (Ananwayee অব্যয়): যে অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন আবেগ, অনুভূতি প্রকাশ করে, তাকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন: হ্যাঁ, না, ছিঃ, বাহ, উঃ, আলবত। উদাহরণ: ছিঃ! তুমি এটা কী করেছো?
- অনুসর্গ অব্যয় (Anusarga অব্যয়): যে অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে বসে শব্দ বিভক্তির মতো কাজ করে, তাকে অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন: দ্বারা, দিয়ে, হতে, থেকে, চেয়ে, পর্যন্ত, অবধি। উদাহরণ: তোমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না।
ক্রিয়া পদ (Kriya Pod): কাজের কথা
যে পদ দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়া পদ বলে। ক্রিয়া মানেই কাজ!
“আমি ভাত খাই” – এখানে “খাই” হলো ক্রিয়া পদ, যা খাওয়ার কাজ বোঝাচ্ছে।
ক্রিয়া পদের প্রকারভেদ (Kriya Pod er Prokarভেদ):
ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়া পদ দুই প্রকার:
- সমাপিকা ক্রিয়া (Samapika Kriya): যে ক্রিয়া পদের দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ, এই ক্রিয়া পদ বাক্য শেষ করতে পারে। যেমন: আমি ভাত খাই। এখানে ‘খাই’ ক্রিয়াটি দ্বারা বাক্যটি সম্পূর্ণ হয়েছে।
- অসমাপিকা ক্রিয়া (Asamapika Kriya): যে ক্রিয়া পদের দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না, বাক্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: আমি ভাত খেতে…। এখানে ‘খেতে’ ক্রিয়াটি দ্বারা বাক্যটি শেষ হয়নি, আরও কিছু শোনার অপেক্ষা থাকছে।
গঠন অনুসারে ক্রিয়া দুই প্রকার:
- মৌলিক ক্রিয়া (Moulik Kriya): যে ক্রিয়া কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই মূল ধাতু থেকে গঠিত হয়, তাকে মৌলিক ক্রিয়া বলে। এগুলোকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয়। যেমন: খা, যা, কর, বল, হ ইত্যাদি। উদাহরণ: আমি ভাত খাই।
- যৌগিক ক্রিয়া (Jougi Kriya): যখন একটি সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন: যেতে দাও, বলতে থাকো, খেয়ে নাও ইত্যাদি। উদাহরণ: তিনি গান গাইতে লাগলেন।
গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (Frequently Asked Questions)
-
প্রশ্ন: পদ চেনার সহজ উপায় কী?
উত্তর: পদ চেনার সহজ উপায় হলো বাক্যে শব্দটির অবস্থান এবং তার অর্থ বোঝা। একটি শব্দ বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
-
প্রশ্ন: বাক্যে পদের অবস্থান পরিবর্তন হলে কি অর্থের পরিবর্তন হয়?
উত্তর: হ্যাঁ, বাক্যে পদের অবস্থান পরিবর্তন হলে অনেক সময় অর্থের পরিবর্তন হতে পারে।
-
প্রশ্ন: ক্রিয়া বিশেষণ ও বিশেষণ পদের মধ্যে পার্থক্য কী?
**উত্তর:** বিশেষণ পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের দোষ, গুণ, অবস্থা বোঝায়। আর ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়া পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, ইত্যাদি প্রকাশ করে।
-
প্রশ্ন: অনুসর্গ অব্যয় এবং সাধারণ অব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: অনুসর্গ অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে বসে শব্দ বিভক্তির মতো কাজ করে, যেমন: ‘দিয়ে’, ‘থেকে’, ‘চেয়ে’ ইত্যাদি। অন্যদিকে, সাধারণ অব্যয় দুটি শব্দ বা বাক্যকে যুক্ত করে, যেমন: ‘এবং’, ‘কিন্তু’, ‘অথবা’ ইত্যাদি। অনুসর্গ অব্যয় সাধারণত কোনো পদের পরে বসে, কিন্তু সাধারণ অব্যয় স্বাধীনভাবে বসতে পারে।
বাস্তব জীবনে পদের ব্যবহার (Practical Application of Pods)
আমরা প্রতিদিন কথা বলার সময়, লেখার সময় অজান্তেই পদ ব্যবহার করছি। সাহিত্য, কবিতা, গান, গল্প – সবকিছুর মধ্যেই পদের ব্যবহার রয়েছে। তাই, ভাষার সঠিক ব্যবহার জানতে হলে পদের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।
- kommunikativ: সংবাদপত্রে নির্ভুল বাক্য গঠনে পদের সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন।
- kreativ: কবিতা বা গান লেখার সময় পদের সঠিক ব্যবহার ছন্দ এবং তাল ঠিক রাখতে সাহায্য করে।
- pedagogisk: শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ শেখানোর ক্ষেত্রে পদের ধারণা দেওয়া জরুরি।
- social: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সঠিক ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পদ সাহায্য করে।
শেষ কথা (Conclusion)
আশা করি, পদের প্রকারভেদ এবং ব্যবহার সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দিতে পেরেছি। ব্যাকরণ ভীতি দূর করে ভাষাকে ভালোবাসুন, ভাষাকে জানুন। বাংলা ভাষার সৌন্দর্য এবং মাধুর্য উপলব্ধি করুন। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে নির্দ্বিধায় কমেন্ট বক্সে জানান। আর হ্যাঁ, এই লেখাটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না!